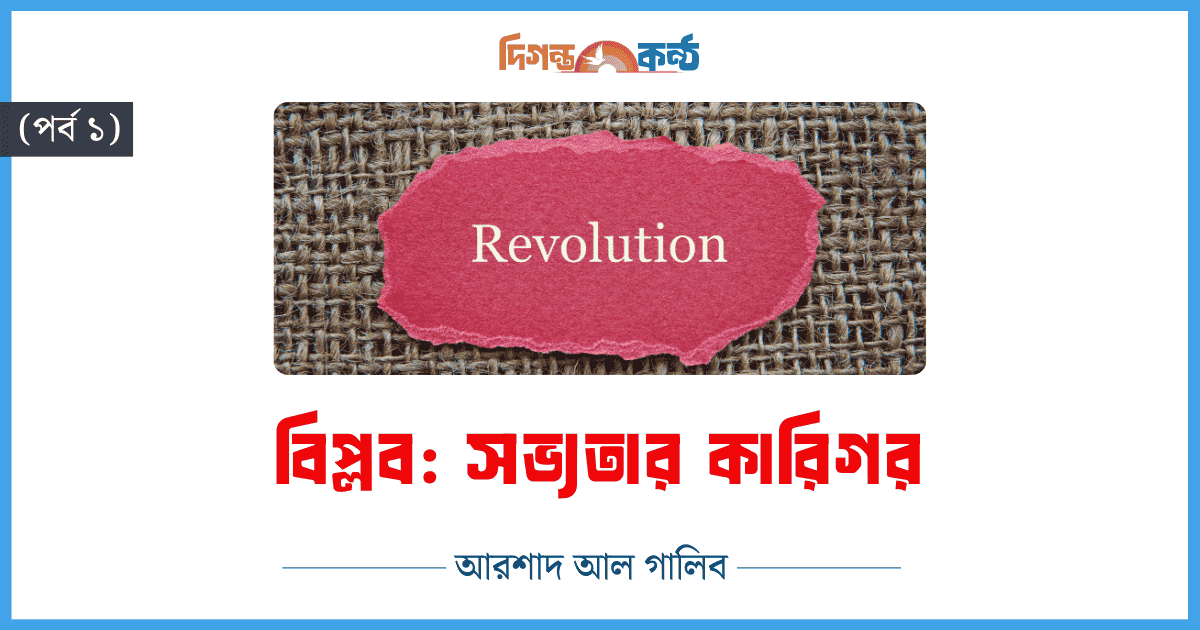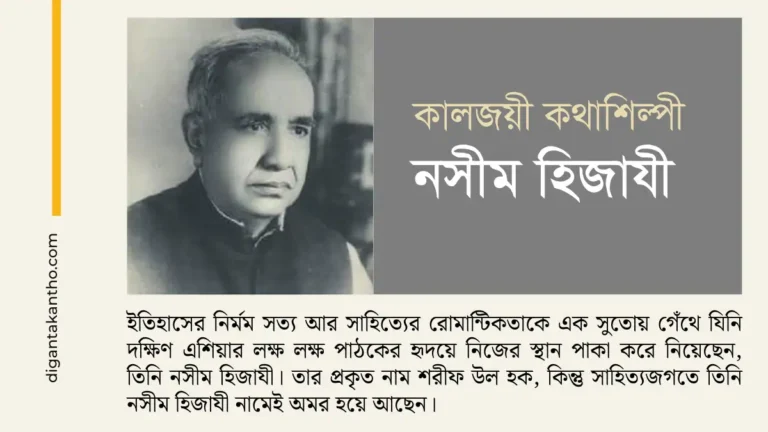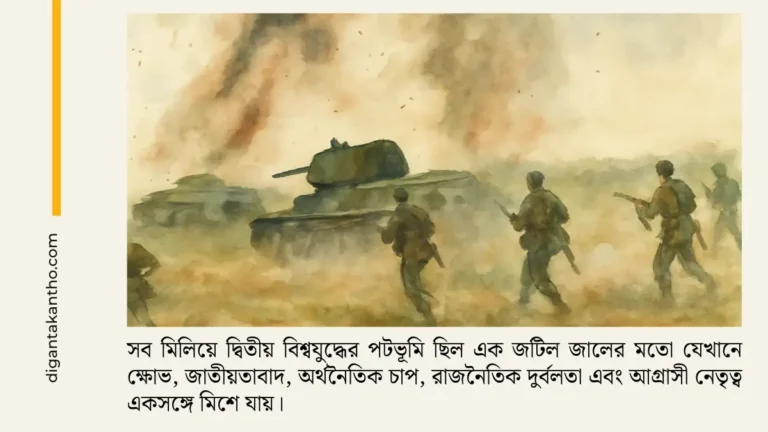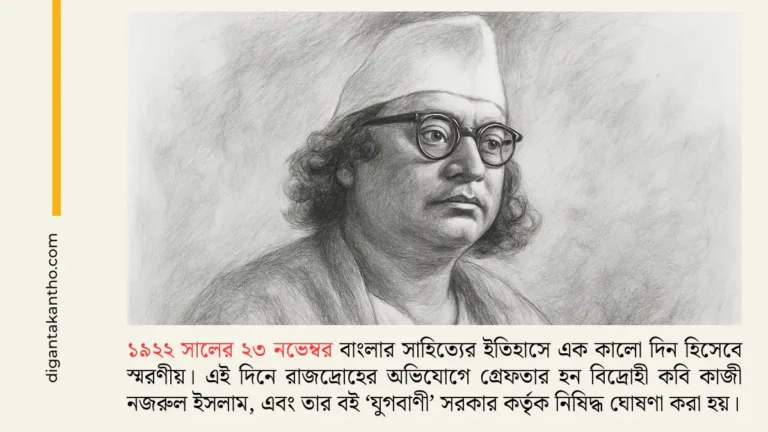বিপ্লব: সভ্যতার কারিগর (পর্ব ১)
আরশাদ আল গালিব
মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিপ্লব এক অনিবার্য সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া। প্রতি যুগেই যখন অন্যায়, বৈষম্য ও শোষণ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, তখনি জনগণ বিদ্রোহ করেছে এবং সেই বিদ্রোহই রূপ নিয়েছে বিপ্লবে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিপ্লব কখনো স্বাধীনতা এনেছে, কখনো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে, আবার কখনো নতুন ধরনের স্বৈরাচারের জন্ম দিয়েছে।
কিন্তু বিপ্লব থেমে থাকেনি। সময়ের প্রয়োজনে জাগ্রত হয়েছে বিপ্লব। তাই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের শুধু অনুপ্রেরণাই দেয় না, বরং জুলুমের প্রতি একটি সুসংহত প্রতিরোধ হিসেবে বিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরির মত প্রজ্বলিত হতে থাকে।
এই ধারাবাহিক লেখার এ পর্বে তুলে ধরবো পৃথিবীর কিছু বিপ্লব যা বদলে দিয়েছে ইতিহাসের দিকপাঠ;
আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৫–১৭৮৩) ছিল প্রচলিত আধুনিক গণতন্ত্রের এক যুগান্তকারী সূচনা। “No taxation without representation” এই স্লোগানকে কেন্দ্র করে উপনিবেশবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এর মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং সংবিধান, নির্বাচনী ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের একটি মডেল তারা তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে স্বাধীনতা ও জনগণের সম্মিলিত অধিকার রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অবশেষে সফলতা আনে।
এই ধারাবাহিকতায় অনেকটা পরপরই আসে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯–১৭৯৯)। মানব ইতিহাসে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটায়। শ্রেণী বৈষম্য, আর্থিক সংকট ও আলোকিত চিন্তার প্রভাবে সাধারণ জনগণ শোষক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। “Liberté, Égalité, Fraternité” বা স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের এক জাগরণী শ্লোগান গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।
তবে জনগণের ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার দাবিতে রাজতন্ত্র উৎখাত হলেও, শীঘ্রই অভ্যন্তরীণ বিভাজন, ক্ষমতার লড়াই এবং প্রতিশোধপরায়ণতা রক্তাক্ত সন্ত্রাসে পরিণত হয়। রবেসপিয়ের ও জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে “রেইনের আতঙ্ক” নামে পরিচিত সময়টিতে হাজার হাজার মানুষকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।
সুতরাং বিপ্লব কেবলমাত্র স্বৈরাচারকে উৎখাত করলেই সফল হয় না বরং ঐক্য, ন্যায়বিচার, এবং পরবর্তী রাষ্ট্রগঠনের জন্য সুসংগঠিত রূপরেখা না থাকলে বিপ্লব নিজেই আত্মবিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। আদর্শিক বিপ্লব যদি সঠিক নেতৃত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারে তবে তা স্বৈরতান্ত্রিক রূপও নিতে পারে। তার বড় একটি উদাহরণ এটি।
হাইতিয়ান বিপ্লব (১৭৯১–১৮০৪) ছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ইতিহাসের এক বিরল উদাহরণ। এটি ছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে একমাত্র সফল গণবিপ্লব, যার মাধ্যমে উপনিবেশিক শক্তি এবং বিশ্বের প্রায় সবশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে। তাই হাইতিয়ান বিপ্লবকে ইতিহাসে এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে হাইতি, যা তখন “সেন্ট ডমিঙ্গু” নামে পরিচিত ছিল, ফরাসি উপনিবেশের অন্তর্গত। এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী উপনিবেশগুলির মধ্যে একটি, কারণ এখানে চিনি ও কফি চাষ দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল হয়ে বিশাল এক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। হাইতির জনসংখ্যার মাত্র ৫% ছিল ইউরোপীয় শাসক এবং ঋণগ্রস্ত স্বাধীন কৃষক। এর বাইরে প্রায় ৯০% মানুষ ছিল আফ্রিকান দাস। দাসদের জীবন ছিল নিষ্ঠুর অত্যাচার, কঠোর শারীরিক শ্রম এবং মানবাধিকারহীনতার এক নির্মম নিদর্শন।
১৭৯১ সালে দাসদের মধ্যে অসন্তোষ চরমে পৌছায়। ফরাসি বিপ্লবের সমতা ও স্বাধীনতার আদর্শ হাইতিতে পৌছে যায় এবং এটি দাসদের মধ্যে আশা জাগায়। তারা একতাবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। দাস নেতারা যেমন টুসঁ লুভারচার (Toussaint Louverture), জঁ জ্যাক দেশালিন (Jean-Jacques Dessalines) এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র স্থানীয় শোষণকারীদের বিরুদ্ধে ছিল না, এটি ছিলো ফরাসি, স্প্যানিশ ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত গণজাগরণ ও বিদ্রোহ।
উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবিতে একের পর এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিশেষত ১৮৪৮ সালের বিপ্লবগুলোকে বলা হয় “Springtime of Nations” ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইউরোপের অনেক ছোট দেশ বিদেশী শক্তির অধীনে ছিল। পোল্যাণ্ড, উত্তর ইতালি, বোহেমিয়া এবং হাঙ্গেরির মতো দেশগুলো দমন করা হলেও, হাঙ্গেরির লোজস কোসুখের নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়াই এবং পরবর্তী দ্বৈত-রাজত্ব প্রমাণ করে যে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব। ফ্রান্সে লুই ফিলিপকে রাজসিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই নেপোলিয়নের ভাইপো লুই বোনাপার্ট সামরিক শক্তি ব্যবহার করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডে বড় বিদ্রোহ না হলেও চার্টিস্ট আন্দোলন শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের অধিকারকে এগিয়ে আনে। এই প্রেক্ষাপট দেখায় বিপ্লবের ব্যর্থতা অনেক সময় সাময়িক হলেও তার একটি প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকে।
১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লব শুরু হয়। দীর্ঘদিনের শাসক জার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যরা একত্রিত হয়ে বোলশেভিকদের নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্র উৎখাত করে। এর ফলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন জন্ম নেয়। এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির অধিকার, সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সমতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। কিন্তু একদলীয় শাসন এবং রাজনৈতিক দমননীতি অনেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত করে। সুতরাং একদিকে সমাজের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হলেও, ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীভূত হলে দীর্ঘমেয়াদে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে।
চীনা বিপ্লব (১৯৪৯) একই রকম উদাহরণ। দীর্ঘ উপনিবেশী শোষণ, অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য ও সামরিক সংঘাতের কারণে সাধারণ জনগণ বিশেষত কৃষক ও শ্রমিকরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সে তুংয়ের তত্ত্বাবধানে আন্দোলনে অংশ নেয়। বিপ্লবের পর চীনা প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে এবং চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লব চীনের হাজার বছরের শাসন ব্যবস্থাকে এক নতুন রূপ দেয় শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সামাজিক সংস্কার, কিন্তু একইসঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাএকচেটিয়াভাবে হওয়ায় কেন্দ্রীভূত শাসন এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।
কিউবান বিপ্লব (১৯৫৯)। ছোট একটি দ্বীপ রাষ্ট্রের জন্য এটি ছিল এক বিরল ঘটনা। ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে বিপ্লব চূড়ান্তভাবে Fulgencio Batista পতন ঘটায়। কিউবা সাম্যবাদী নীতি গ্রহণ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ খাতে বড় পরিবর্তন আনে। এছাড়াও, এটি দেখায় ছোট রাষ্ট্রও যদি একক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়, বৈশ্বিক শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। তবে, একদলীয় শাসন, মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকটও দীর্ঘমেয়াদে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে।
ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি পশ্চিমাপন্থী শাসক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু দেশজুড়ে দুর্নীতি, স্বৈরশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন জনগণের ক্ষোভ তৈরি করে। আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইরান ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
ইরান শরীয়া আইনে পরিচালিত ধর্মীয় নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে ইসলামি আইন (শরিয়াহ) সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। তবে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে সংঘাত, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক সংকটও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
তিউনিশিয়ার এক ফল বিক্রেতা মোহাম্মদ বুয়াজিজির আত্মাহুতি থেকেই আরব স্প্রিংয়ের সূচনা হয়। দুর্নীতি, বেকারত্ব, স্বৈরশাসন ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে এটি একটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিউনিশিয়া, মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া সহ বহু দেশে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিশিয়ায় গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু মিশরে সামরিক শাসন ফিরে আসে, লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ এবং সিরিয়ায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কিছু দেশে পরিবর্তনের আশা জাগলেও বেশিরভাগ দেশে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল আলজেরিয়া। দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আলজেরীয়রা মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ আলজেরীয় প্রাণ দেয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স পরাজিত হয় এবং স্বাধীন আলজেরিয়ার জন্ম হয়। স্বাধীনতা অর্জন হলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামরিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেশকে স্থায়ী শান্তি ও সুশাসন দিতে ব্যর্থ হয়।
দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসক ওমর আল-বশির দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট ও দমননীতির কারণে জনগণের ক্রোধের মুখে পড়েন। ব্যাপক গণআন্দোলন শেষে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। জনগণের আশা ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামরিক বাহিনী পুনরায় ক্ষমতা দখল করে নেয়। সামরিক-নাগরিক দ্বন্দ্বের কারণে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা থমকে যায়। তাই স্বৈরশাসকের পতনই শেষ লক্ষ্য নয়, বরং নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
সার্বিকভাবে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে, কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হলো জনগণের ঐক্য। যেকোনো বিপ্লবের স্থায়ী সাফল্য নির্ভর করে সঠিক নেতৃত্ব, সুসংগঠিত পরিকল্পনা ও স্পষ্ট লক্ষ্যর ওপর। পাশাপাশি, ইতিহাস প্রমাণ করে প্রতিটি বিপ্লব স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, ফলে ফলাফলও ভিন্ন হতে পারে। এই শিক্ষাই স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, বিপ্লব কেবল স্লোগান বা মুহূর্তের উচ্ছ্বাস নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া, যেখানে আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই প্রকৃত সাফল্য।
এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী পর্বে বিশদভাবে ধরা হবে বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব ২০২৪। এটি দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা হিসেবে ধরা হচ্ছে। পাঠকবৃন্দের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্ববহ, তাই আগামী পর্বে ঘটনার বিশদ বিবরণ ও প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করার জন্য অপেক্ষায় থাকুন।
তথ্যসূত্র:
১) বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ/বিপ্লব, এবং বিশেষ করে ইউরোপে ১৮৪৮ সনের বিপ্লব https://tinyurl.com/yuauf8je
২) ফরাসি বিপ্লব : https://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2855/Unit-02.pdf
৩) ইউরোপের ইতিহাসে বিপ্লব এবং শিল্প সমাজের বিকাশ, ১৭৮৯-১৯১৪ :
https://www-britannica-com.translate.goog/topic/history-of-Europe/The-age-of-revolution
৪) বিশ্বের ইতিহাস পাল্টে দেয়া কয়েকটি গণ আন্দোলন :
https://archive.roar.media/bangla/main/history/protests-in-the-world-that-changed-the-history
৫) আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব – মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
https://www.icsbook.info/read-book/323